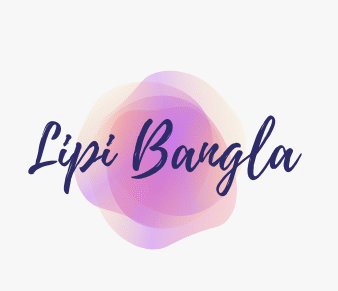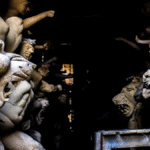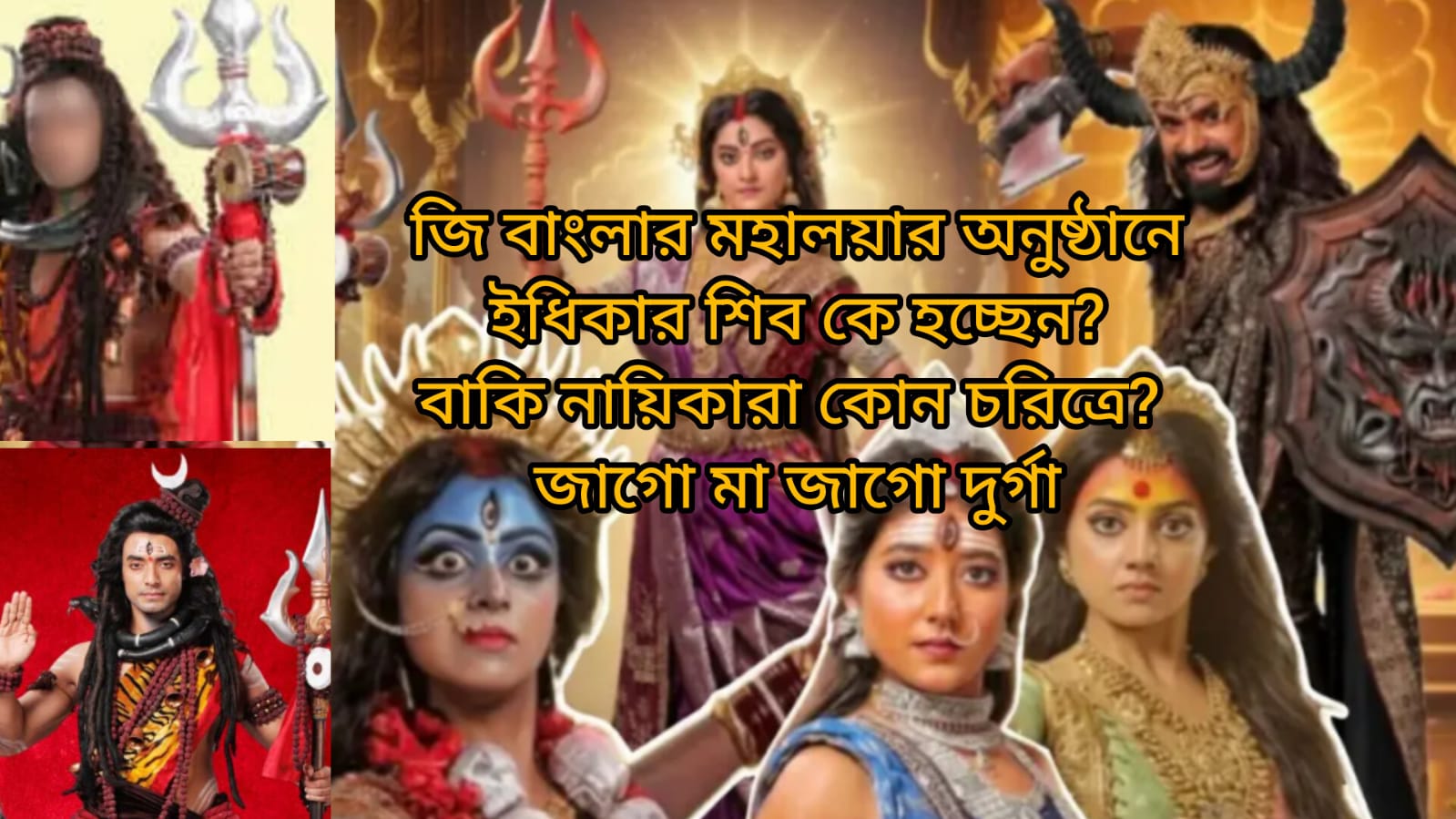নয়, তিনি পৌরাণিক কল্পনায় সীমাবদ্ধ নন Durga Puja 2025
কলকাতার সন্ধ্যায় কাশফুলে ভরা আকাশের নীচে যখন দুর্গাপূজার আবির্ভাব ঘটে, তখন আমাদের বুকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের স্ফুরণ ঘটে না—সঙ্গে জাগে এক গভীর আত্মিক বোধ। এই বোধ এমন এক দেবীর মুখের প্রতিচ্ছবি, যিনি শুধু পুরাণের চরিত্র নন; তিনি আমাদের মাটি, আমাদের মেয়েরা, আমাদের মা, এবং আমাদের আদি জীবন, এই সব কিছু মিলিয়ে বিচ্ছিন্ন এক ইতিহাসের কণ্ঠ।
দুর্গার আদিবাসী ও লোকমুখো নির্মাণ, যেমন টুসু উৎসবের মাটির পুতুল, ছৌ মুখোশ, চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নকর্ম—এই সবের মধ্যেই মেলে সেই আদম মুখের নিদর্শন। সেখানে ঠোঁটে সূক্ষ্মতা, গালে চাপা ও ঠান্ডা ছাপ, অঙ্ক কালো ভ্রু—সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক “লোকায়ত দৃষ্টিদান”। এ মুখ কল্পনার নয়—এটি বাস্তবের, মাটির, মানুষের।
আদিম জনজাতির শিল্প ও দেবীর আদলে রূপান্তর
চুয়ার দেশ—আজ আর্যাবর্তীয় পশ্চিমবঙ্গ-ঝারখণ্ডের লাল মাটির অঞ্চল—তখন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংকর এক জনজাতির আবাসস্থল ছিল, যারা মাতৃতান্ত্রিক পূজায় নারীদের কেন্দ্রে রেখেছিল। তাদের বর্সায় আলপনা, শস্যে পূজা, মাটির পুতুলের মাধ্যমে নারীর শক্তি আরাধনা—সেই রূপ থেকেই উদ্ভূত হয় দুর্গাপ্রতিমার আদিম আদল। নবম শতকে রাজার সংস্পর্শে পৌঁছে সেই মুখ হয়ে ওঠে রাজপথের মূর্তি, তথাপি মুখে রয়ে যায় সেই শেকড়ের ছাপ।
লোকায়ত থেকে রাজঘর—দেবীর বিবর্তন
১৫৮২ সালে গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ, রাজসূয় বা অশ্বমেধের বিপরীতে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করে, সেখানে তারা যে নারীর কিছু গড়ার রীতি মেনে চললেন, তা ছিল আদিবাসী আত্মশৈলীর একটি স্থায়ী ছাপ। তখন যা তৈরি হলো—সে ছিল রাজআদল, কিন্তু মুখে ছিল ছউ-নাচ, টুসুর রূপ। এভাবেই মহিলা শক্তি রাজ ঘরে প্রবেশ করল, অথচ লোকায়তত্ব ধরে রাখল।
প্রত্নতত্ত্ব ও লোকজ ঐতিহ্যের মিলন
চন্দ্রকেতুগড়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বর্ধমান, পুরুলিয়া—এ ধরনের প্রত্নস্হানে পাওয়া মা-মূর্তি সেই বিবর্তিত সংস্কৃতির সাক্ষী। এখানে দেখা যায়, দেবী কখন শস্যদাত্রী, কখন গৃহলক্ষ্মী, আবার কখন মহিষমর্দিনী—পুরাণ ও জনজীবনের মিলন, এক স্থায়ী দায়বদ্ধতায় বিশ্লেষণ।
লোকজ উৎসব যেমন টুসু ও ছৌ-নাচ সেই মূর্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে—টুসু উৎসবে মায়েরা মাটির মুখে নিজস্ব মুখ খুঁজে, আর ছৌ মূর্তিতে দেখা যায় এক গভীর রুদ্রতা-কৌমার্য মিশ্রণ। সব মিলিয়ে দেবীর মুখ স্থান পেয়েছে আমাদের লোকসাহিত্য, শিল্প ও জনজীবনের প্রকট চেতনায়।
সাংস্কৃতিক বিপ্লব — “চুয়ার মুখই দুর্গার মুখ”
এই এক সত্য: দুর্গাপূজা কেবল তন্ত্র-আচার নয়, তা ছিল আদিবাসী নারীর মা-শক্তির রাজনীতি। যেখানে নারী ছিলেন সমগ্র সমাজের জীবনীশক্তি—পুতুল, রানী, শস্য, নদী—সবকিছুর মা। সেই শক্তি রাজবংশের শাসনাধীনে ঢুকে গেলেও, সেই চুয়ার মুখের আদিম তেজ আত্মিকভাবে অপরিবর্তিত রয়ে গেল।
শেষে আমাদের দেখতে হয়, আজকের দুর্গার মুখ হয়তো শীতল, নিটোল, পরিপাটি—কিন্তু তার ভিতরে কি সেই তেজস্বিনী আদিম মা রয়ে গেল? আদিবাসী পুতুলের, টুসু-নৃত্যের, ছৌ-নৃত্যের সেই শক্তি এখনও কি বজায় আছে? বা আমরা তাকে সুরঙ্গ করে ফেলেছি নানাবিধ সাজে?
আজকের দুর্গা শুধু দেবদেবী নয়—তিনি আমাদের নিজের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর জনজীবনের এক প্রতিচ্ছবি। প্রতিমা হয়তো চকচকে, কিন্তু সেই চমকসারি মুখের নিচে লুকিয়ে থাকে লালমাটির আদিম তেজ। তিনি সেই মা, যিনি সঙ্গে আঁকেন গল্প, গণমঙ্গল, শিল্প, প্রতিরোধ, প্রেম আর রূপ। দুর্গাপূজা তাই শুধু ধর্ম নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও জনজন্মের এক উদযাপন—যেখানে দেবীর মুখ আসলে আমাদের মুখ, সেই ভাঙা, আদিম, চেতনাময় মুখ।