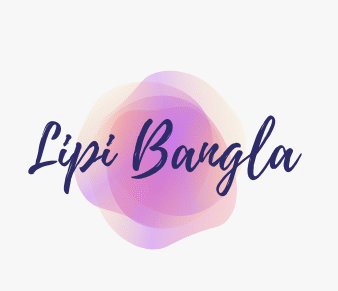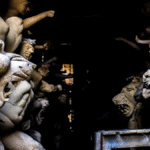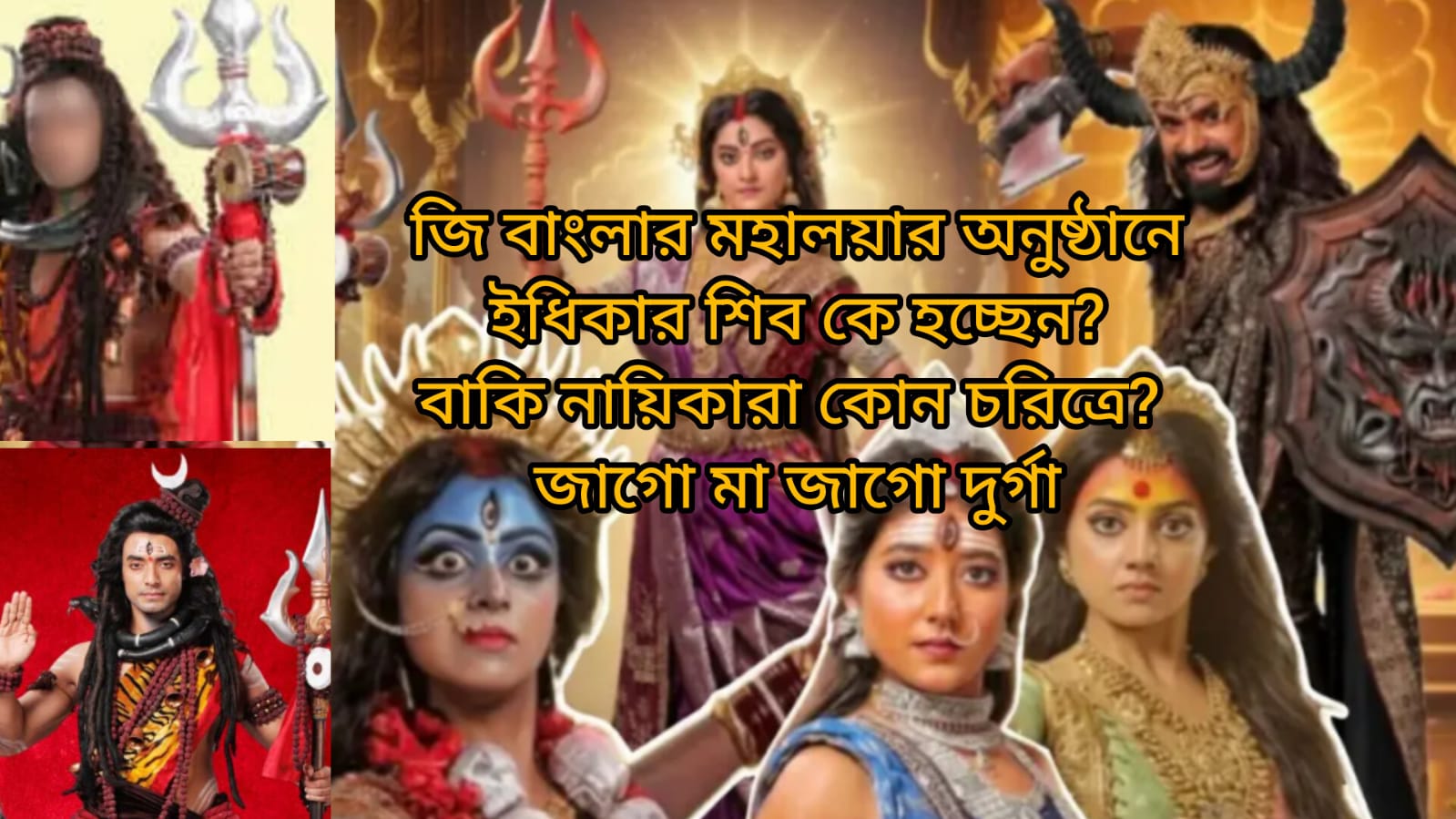পিতৃপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি সমাজের বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুভূতি, পারিবারিক বন্ধন আর পুরাণকথার গভীর তাৎপর্য। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা থেকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পর্যন্ত এই সময়টাকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক আত্মিক সংযোগের মুহূর্ত হিসেবে দেখা হয়। মানুষ ভাবে, এই সময়ে পূর্বপুরুষেরা মর্ত্যে নেমে আসেন, তাঁদের জন্য তর্পণ করা, পিন্ডদান, ব্রাহ্মণভোজন কিংবা কাককে খাওয়ানো আসলে এক ধরনের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।
পিতৃপক্ষ ২০২৫: আমরা যখন ‘পিতৃপক্ষ’ শব্দটি শুনি, তখন প্রথমেই মনে হয়, এটা একটা দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন মাত্র। কিন্তু বিষয়টা তার থেকেও অনেক বড়। মানুষ জন্মগতভাবেই নিজের শিকড়ের প্রতি টান অনুভব করে। বাবা-মা, দাদা-দিদা, প্রপিতামহ—এই শিকড়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই হয়তো এই বিশেষ সময়ের প্রয়োজন। যখন কেউ তার বংশের মৃত মানুষদের স্মরণ করে, তখন সে আসলে নিজের অস্তিত্বকেই নতুন করে উপলব্ধি করে।
পুরাণের কর্ণের কাহিনি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারাজীবন দানধ্যান করে যাওয়া কর্ণ যখন স্বর্গে পৌঁছালেন, সেখানে তাঁকে সোনা-রত্ন দেওয়া হলো, কিন্তু খাদ্য নয়। কেননা তিনি জীবিত অবস্থায় কখনও পূর্বপুরুষকে তর্পণ করেননি। এখানেই বোঝা যায়, কেবল দান নয়, পূর্বপুরুষকে স্মরণ করা জীবনের এক অপরিহার্য কর্তব্য। ইন্দ্র তাঁকে মর্ত্যে ফিরে আসার সুযোগ দেন—এ যেন মানুষের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রতীকী কাহিনি। আমাদের জীবনে যে কর্তব্য আছে, তা এড়িয়ে গেলে পরে তার দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন।
ভীষ্মের কাহিনি থেকে পিতৃপক্ষের অন্য দিকটি বোঝা যায়। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম অপেক্ষা করেছিলেন উত্তরায়ণের জন্য। দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ কেবল সূর্যের গতি নয়, মানুষের বিশ্বাসে জীবনের গতি। ভীষ্মের মৃত্যু বেছে নেওয়ার মুহূর্ত, তাঁর ধৈর্য, তাঁর ইচ্ছামৃত্যুর বর আসলে আমাদের শেখায়—সময়ের গুরুত্ব কতটা। পিতৃপক্ষ আসলে সেই ‘সময়’-এর এক স্মরণ। মৃত্যু আর জীবনের মাঝামাঝি যে সেতু, পিতৃপক্ষ সেখানে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষকে ডাকে।
শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীবিত মানুষের আগের তিন প্রজন্ম পিতৃলোকে থাকেন। এই ধারণা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও আকর্ষণীয়। কেন তিন প্রজন্ম? হয়তো তার কারণ এই যে, আমাদের চিন্তাভাবনা, সংস্কার, জীবনযাপনের ধরন আসলে তিন প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়। পিতৃপুরুষকে শ্রাদ্ধ করার মানে হলো, আমরা সেই ধারাবাহিকতাকে সম্মান জানাচ্ছি। যম, মৃত্যুর দেবতা, এই সংযোগের পথিকৃত। তিনি আত্মাকে নিয়ে যান, আবার আমাদের তর্পণের মাধ্যমে আত্মার শান্তিও নিশ্চিত করেন।
কাককে খাওয়ানোর রীতি নিয়ে ভাবলে দেখা যায়, লোকবিশ্বাস ও প্রতীকী ধারণা এখানে একসঙ্গে কাজ করছে। কাককে পূর্বপুরুষের প্রতিরূপ ধরা হয়। কেন? কারণ কাক দীর্ঘায়ু, সর্বভুক, দূরদূরান্তে ভ্রমণ করতে পারে এবং প্রায় সর্বত্র টিকে থাকে। কাককে তাই এমন এক প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের আত্মা আমাদের ঘরে আসে। সীতার কাহিনিতে জয়ন্ত কাকের রূপ নিয়েছিল। পরে রামের আশীর্বাদে কাক হয়ে উঠল পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি। এই গল্প শুনলে বোঝা যায়, ধর্মগ্রন্থ কেবল কাহিনি নয়, এর মধ্যে প্রতীকী ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে।
তবে পিতৃপক্ষ শুধু কাককে নয়, গরু, কুকুর, এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুকেও খাওয়ানোর নিয়ম করে দিয়েছে। এতে বোঝা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। খাদ্য যদি প্রাণীগ্রহণ করে, তবে ধরে নেওয়া হয় পূর্বপুরুষ তা গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্কই চূড়ান্ত সত্য।
একটা দারুণ দার্শনিক দিক হলো—পিতৃপক্ষ আসলে মৃত্যু-চিন্তার মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার সময়। বাঙালির জীবনে এই সময়টা দেবীপক্ষের আগমনের প্রহর গোনারও সময়। অমাবস্যায় পিতৃপক্ষ শেষ হয়, আর পরদিন থেকেই দেবীপক্ষ শুরু হয়। অর্থাৎ মৃত্যু ও জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ পূজো-পার্বণের আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদিক থেকে এটা মৃত্যুর বেদনার মধ্যে জীবনোৎসবের জয়গান।
অত্রি ঋষির বংশধর নিমির কাহিনি এখানেও তাৎপর্যপূর্ণ। পুত্রশোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আত্মার মৃত্যু হয় না। তাই শ্রাদ্ধকর্ম শুরু হয়েছিল শান্তির উদ্দেশ্যে, মুক্তির উদ্দেশ্যে। এটা আসলে আমাদের জন্য এক শিক্ষা—আমরা যাদের হারাই, তাঁরা কেবল দেহে অনুপস্থিত, কিন্তু আত্মায় থেকে যান। তাঁদের শান্তির জন্যই আমাদের তর্পণ, আমাদের প্রার্থনা।
পিতৃপক্ষকে যদি সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা যায়, তবে বোঝা যায়, এই সময়টা পরিবারের মধ্যে ঐক্যের মুহূর্ত। বাড়ির সবাই মিলে পিতৃপক্ষ পালন করে। এতে বংশধরদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। আবার আত্মীয়তার নেটওয়ার্কও নতুন করে জোরদার হয়। পূর্বপুরুষকে স্মরণ করতে গিয়ে মানুষ নিজের সমসাময়িক প্রজন্মকেও নতুনভাবে উপলব্ধি করে।
মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এর বড় তাৎপর্য আছে। মৃত্যু আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য সত্য। কিন্তু মানুষ সবসময় মৃত্যু এড়িয়ে বাঁচতে চায়। পিতৃপক্ষ আসলে সেই অস্বস্তিকে সহজ করে দেয়। এই সময়ে মানুষ মেনে নেয় যে মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু সেই মৃত্যুও জীবনের এক ধারাবাহিকতা। পূর্বপুরুষের আত্মা শান্ত হলে বর্তমান প্রজন্মও আশীর্বাদ পায়—এই বিশ্বাস মানুষের ভয় কমায়।
আজকের আধুনিক সমাজেও পিতৃপক্ষের গুরুত্ব কমেনি। হয়তো অনেকে আচার পালনে নিয়মিত নন, কিন্তু শিকড়ের প্রতি টান, পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার ইচ্ছা আজও প্রবল। মানুষ ভাবে—আমি আজ যা পেয়েছি, তা আমার আগের প্রজন্মের পরিশ্রম, ত্যাগ আর আশীর্বাদের ফল। এই ভাবনা থেকেই পিতৃপক্ষ আজও প্রাসঙ্গিক।
সবশেষে বলা যায়, পিতৃপক্ষ কেবল মৃতদের স্মরণ নয়, জীবিতদেরও এক গভীর শিক্ষা দেয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভালোবাসা, কর্তব্য, সম্পর্ক এগুলোই আমাদের শিকড়। সেই শিকড়ের জলসেচনই হলো পিতৃপক্ষ। শ্রাদ্ধ আর তর্পণের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন বার্তা—আমরা যেন আমাদের শিকড় ভুলে না যাই, কারণ শিকড়ই আমাদের জীবনের শক্তি।